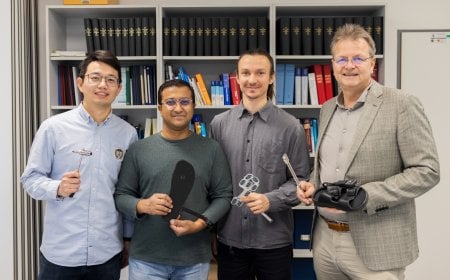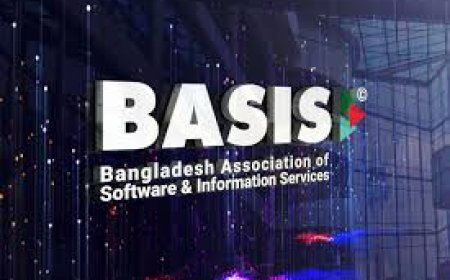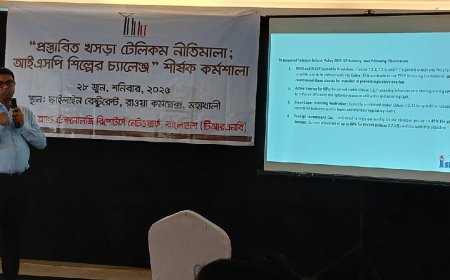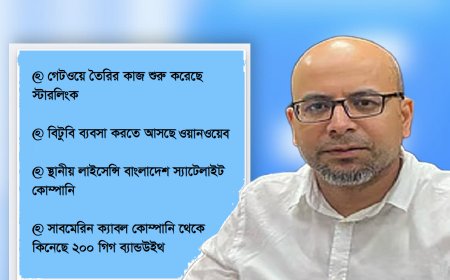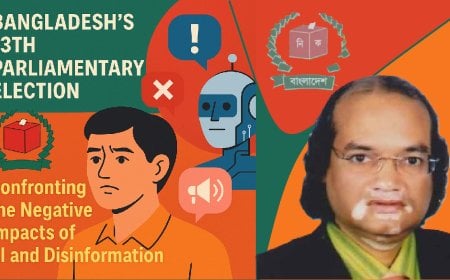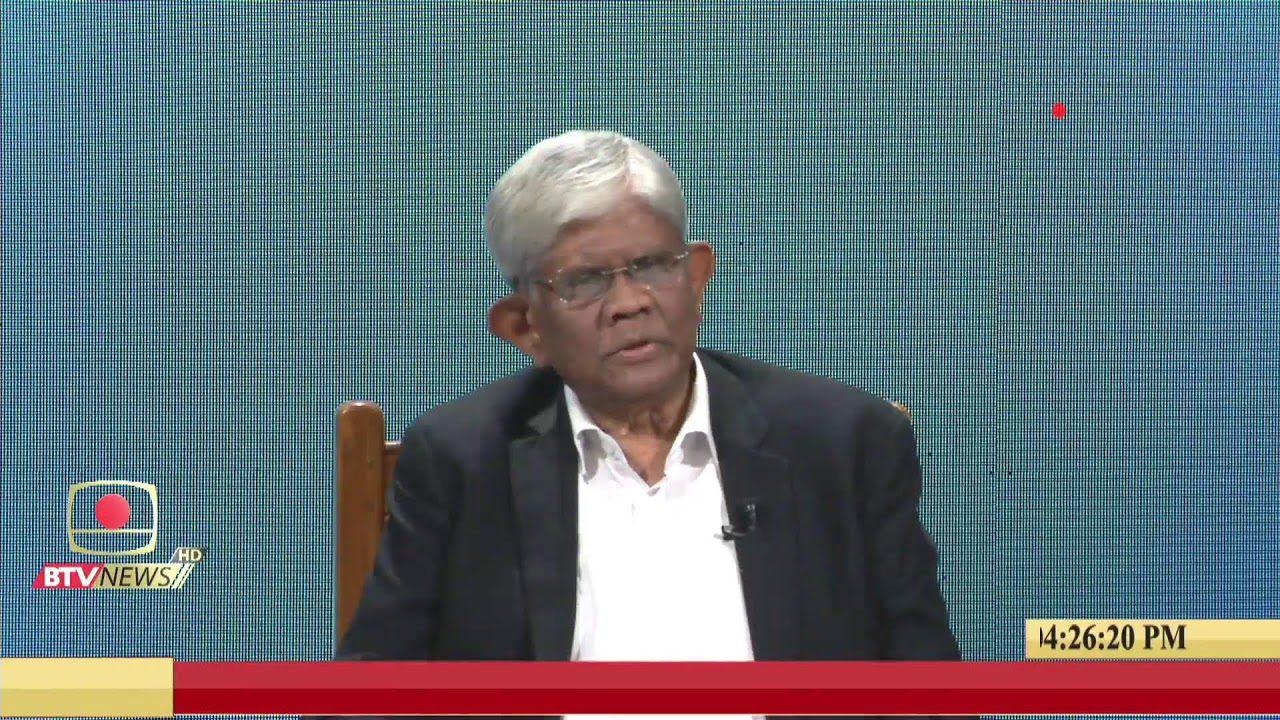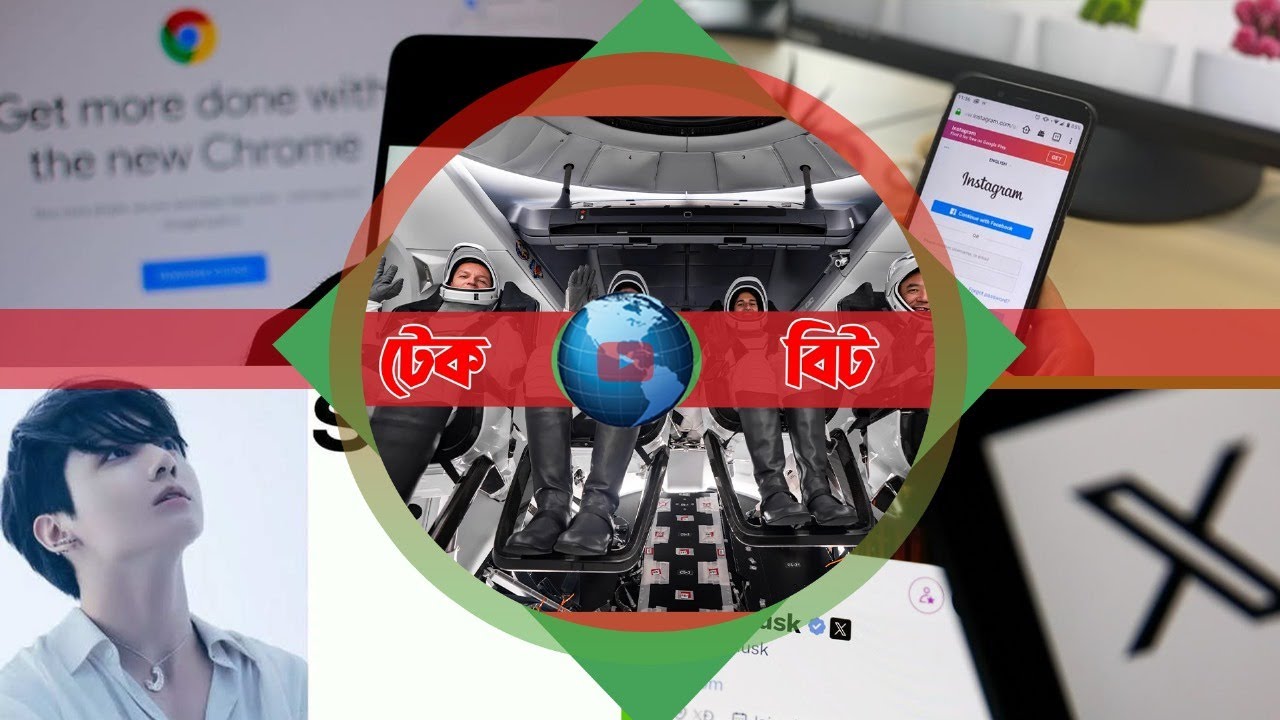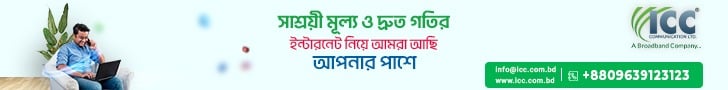টেলিকম খাত সংস্কার : সমসাময়িক ভাবনা

সম্প্রতি বিটিআরসি নেটওয়ার্ক টপোলজি ও লাইসেন্সিং রেজিম শিরোনামে টেলিকম নীতিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তড়িঘড়ি করে দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রস্তাবিত টপোলজি বিদ্যমান টেলিকম লাইসেন্সধারীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে, যেখানে একতরফাভাবে আইজিডব্লিউ (IGW), আইসিএক্স (ICX), আইআইজি (IIG) এবং অন্যান্য বেশকিছু দেশীয় লাইসেন্স বাতিল করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং বেশির ভাগ লাইসেন্স এমএনও (MNO) অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি মূলত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে একটি ‘ইউনিফাইড লাইসেন্স’ দেওয়ার আরেকটি রূপ।
উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে প্রণীত আইএলডিটিএস (ILTDS) নীতির মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ করা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে গত দুই দশকে বাংলাদেশের টেলিকম খাত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে, যেখানে সেবার মান বা জাতীয় স্বার্থের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। সব লাইসেন্সধারীরা তাদের অবকাঠামো নিয়মিত উন্নত করেছে এবং ৫জি ও অন্যান্য উন্নত ডেটা পরিষেবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যৎ প্রস্তুত প্রযুক্তিতে পুনঃবিনিয়োগ করেছে। ডিজিটাল রূপান্তরের প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে কোনো বড় ধরনের নিয়ন্ত্রক বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যখন সফলভাবে পূরণ হচ্ছে, তখন হঠাৎ এই ধরনের পরিবর্তন হতাশাজনক এবং বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার ইঙ্গিত বহন করে।
সাম্প্রতিক এই কর্মশালাগুলোতে ‘থিঙ্কট্যাঙ্ক’, শিক্ষাবিদ এবং বহিরাগত পরামর্শকদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এরা টেলিকম নেটওয়ার্ক টপোলজিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করেছে, যা দেশীয় উদ্যোক্তাদের সরিয়ে দেবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনে কোনো গভীর বিশ্লেষণ বা বিদ্যমান লাইসেন্সধারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কোনো স্বীকৃতিই নেই। উল্লেখ্য, অন্য কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি স্তর বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল শুধু মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নয়, বরং মূল জাতীয় অবকাঠামো হিসেবে, যা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেছে : (১) কাঠামোবদ্ধ আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্ক কনজেশন কমানো। (২) কল ডিটেল রেকর্ড (ঈউজ) ও ডেটা ট্রাফিকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা (৩) টেলিকম খাতে হাজারো তরুণ প্রযুক্তি পেশাজীবীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। (৪) সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ২০০৮ সালে যেখানে সরকারি রাজস্ব ছিল ৩,৬০০ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৮ সালে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৫০,০০০ কোটি টাকায়। আন্তর্জাতিক ভয়েস ট্রাফিক উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও এই নীতির কারণে বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৫৭,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।
যদি বিদ্যমান লাইসেন্সধারীরা আইএলডিটিএস নীতির সব লক্ষ্য সফলভাবে পূরণ করে থাকে, বিটিআরসির সব বিধিবিধান অনুসরণ করে থাকে এবং টানা দুই দশক নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে থাকেÑ তা হলে কেন হঠাৎ করে একটি নতুন টপোলজির প্রয়োজন পড়ছে, যা শিল্পকে অস্থিতিশীল করবে, অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে এবং হাজারো টেলিকম পেশাজীবীকে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে ফেলবে?
পুরো আলোচনা ও কর্মশালায় এটি স্পষ্ট ছিল যে, নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এমএনও (বেশির ভাগ বিদেশি অপারেটর) পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। কর্মশালায় বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও (শুধু এমএনও ছাড়া) বিটিআরসি অবাক করে ঘোষণা দেয় যে, ‘প্রস্তাবিত নেটওয়ার্ক টপোলজি নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।’ এ ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতা উল্লেখ করা প্রয়োজন :
(ক) আইএলডিটিএস নীতি এমএনওদের জন্য একমাত্র বাধা ছিল, যা তাদের সমগ্র টেলিকম বাজার দখল করতে দেয়নি। (খ) এই নীতি এমএনওদের গেটওয়ে, অবকাঠামো বা আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো উপস্থিতি রাখতে দেয়নি। (গ) ইন্টারকানেকশন (ওহঃবৎপড়হহবপঃরড়হ) সুবিধা এমএনওদের অনিয়মের কারণে তাদের থেকে সরিয়ে নিয়ে স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছিল।
বলার অপেক্ষা রাখে না, টেলিকম খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মানোন্নয়নের অন্যতম কারণ হিসেবে এই সংস্কারের অজুহাত দেওয়া হচ্ছে। তবে কিছু বিষয় বিবেচনা করা জরুরি : যেমন- প্রথমত, এমএনওদের অন্যান্য খাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া মানেই দক্ষতা বৃদ্ধি হবে না। কারণ তাদের মোবাইল পরিষেবাই আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেনিÑ উচ্চ চার্জ, কল ড্রপ, নেটওয়ার্ক সমস্যা নিত্যদিনের ঘটনা। তারা নিজস্ব খাতে দক্ষতা আনতে পারেনি, তা হলে অন্যান্য খাতে কীভাবে দক্ষতা আনবে? দ্বিতীয়ত, টেলিকম সেবার মূল চ্যালেঞ্জগুলো আসে মূলত অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস (অঘঝ) অপারেটরদের সীমাবদ্ধতার কারণে, যা এমএনওদের দায়। তৃতীয়ত, এমএনওরা মোট টেলিকম রাজস্বের প্রায় ৮০% আয় করে, ফলে উন্নয়ন প্রয়োজন হলে সেটি এমএনও খাতেই হওয়া উচিত।
সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন উঠতে পারে : প্রথমত, বর্তমান টেলিকম কাঠামোর ত্রুটি বিশ্লেষণ করে কি কোনো গবেষণা করা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তা হলে সেটি কেন প্রকাশ করা হয়নি?
দ্বিতীয়ত, সাধারণত কোনো বড় পরিবর্তনের আগে স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি, বরং একটি পূর্বনির্ধারিত কাঠামো চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা গেছে।
তৃতীয়ত, বিদ্যমান কাঠামো পরিশোধন করে একীভূতকরণের পথে এগোনোর পরিবর্তে নতুন পরিবর্তন কেন?
পরিশেষে, টেলিকম লাইসেন্সিং ব্যবস্থার সংস্কারের আগে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন-
এক. আমাদের দীর্ঘমেয়াদি টেলিকম পরিকল্পনা কী? আমরা কি প্রতিটি স্তরে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (ঋউও) দিয়ে দ্রুত উন্নতি চাই, নাকি ধীরে ধীরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে বিদেশি কোম্পানিগুলোর নির্ভরতা কমাতে চাই?
দুই. যদি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেওয়া হয় (যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক), তা হলে সরকার কী কৌশল নেবে? এই কৌশলই লাইসেন্সিং ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে।
তিন. বর্তমান লাইসেন্স ব্যবস্থার ওপর একটি বিশদ গবেষণা প্রয়োজন, যা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে একচ্ছত্র আধিপত্য দেওয়ার পরিবর্তে এটি জাতীয় স্বার্থের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।
লেখক : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাটেল গ্রুপ